বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশের অবস্থান এখন অষ্টম। যদিও রফতানি আয়ের দিক থেকে বৈশ্বিক তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে এই দেশ।
বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার দিক থেকে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বার্ষিক রফতানি আয় ১০০ বিলিয়ন ডলারের নিচে কেবল তিনটি দেশের, যার অন্যতম বাংলাদেশ।
অপর দেশ দুটি হলো- যথাক্রমে পাকিস্তান ও নাইজেরিয়া। এমনকি এশিয়ার উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ এখনো রফতানিতে বেশ পিছিয়ে।
বিশ্লেষকদের মতে, একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো রফতানি। বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোয় রফতানির অবদানও বেশ বড়। এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলোও রফতানির দিক থেকে এখন বেশ ভালো অবস্থানে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জনগোষ্ঠীর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এসব দেশ এখন নিজ নিজ রফতানিকে সমৃদ্ধ করছে।
এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও সার্বিক রফতানির পরিমাণ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। মূলত নীতি দুর্বলতা ও বড় জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে না পারার কারণেই এ খাতে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না।
বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের রফতানির পরিমাণ ও জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, তুলনামূলক কম জনসংখ্যা নিয়েও রফতানিতে ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে বেশকিছু দেশ। অপর দিকে বড় জনগোষ্ঠীর সুবিধা কাজে লাগানোর মাধ্যমে রফতানিকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে ১৭ কোটি ৩৬ লাখ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী- সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখান থেকে রফতানি হয়েছে ৪৫ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলারের। আর ২০২৩ সালে ১০ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশের চেয়ে আট গুণেরও বেশি রফতানি করেছে ভিয়েতনাম।
দেশটির মোট রফতানির পরিমাণ ৩৭৪ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। মাত্র ৩ কোটি ৫৬ লাখ জনসংখ্যার দেশ মালয়েশিয়া ২০২৩ সালে রফতানি করেছে ২৭৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও সেবা। ১১ কোটি ৫৮ লাখ জনসংখ্যার দেশ ফিলিপাইনের রফতানির পরিমাণ ১১৬ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার। ২৮ কোটি ৩৫ লাখ জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া একই সময়ে পণ্য ও সেবা রফতানি করেছে ২৯৮ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলারের।
বৈশ্বিক জনসংখ্যায় শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য যে দুটি দেশের রফতানি এখনো ১০০ বিলিয়ন ডলারের নিচে, সেগুলো হলো পাকিস্তান ও নাইজেরিয়া। এর মধ্যে ২৫ কোটি ১৩ লাখ জনসংখ্যার দেশ পাকিস্তানের রফতানি ২০২৩ সালে ছিল ৩৫ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। আর একই সময়ে ২৩ কোটি ২৭ লাখ জনসংখ্যার দেশ নাইজেরিয়ার পণ্য ও সেবা রফতানি করেছে ৫৭ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের।
বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গত বছরের সেপ্টেম্বরে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। সম্প্রতি এ টাস্কফোর্স তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের জনসংখ্যা ও রফতানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এ টাস্কফোর্সের সদস্য ও রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যা পিড) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বলেন, সমজাতীয় অন্যান্য অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটি হয়নি।
এর কারণ হচ্ছে রফতানির ক্ষেত্রে নগদ প্রণোদনা ছাড়া সরকারের যেসব নীতি রয়েছে, সেগুলো এ খাতের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সে তুলনায় স্থানীয় বাজারের জন্য তৈরি করা পণ্যের উৎপাদকরা অনেক বেশি সুবিধা পান। আমাদের এখানে প্রতি বছর মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। সেই সঙ্গে মূল্যস্তরও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের চেয়ে বেশি।
একটা সময় বলা হয়েছিল বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে বেশি। এটি কিন্তু ডলারের হিসাবে। কিন্তু আমরা যদি ক্রয়ক্ষমতা সমতার (পিপিআই) ভিত্তিতে এটি হিসাব করি, তাহলে ভারতের মাথাপিছু আয় আমাদের চেয়ে বেশি।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মূল্যস্তর বেশি হওয়ার কারণেই এটি হচ্ছে। মূল্যস্তর বেশি হওয়ার পেছনে উচ্চ শুল্ক হার, দুর্নীতি, ব্যবসা পরিচালনার খরচের মতো বিষয়গুলো জড়িত।
আমরা হিসাব করে দেখেছি স্থানীয় বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনকারীরা যে পরিমাণ সুবিধা পান, তার তুলনায় ৩০ শতাংশ কম প্রণোদনা দেয়া হয় রফতানিতে। আবার রফতানির ক্ষেত্রে কঠোরভাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক।
এর কারণেও স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রিতে লাভ বেশি। ফলে উদ্যোক্তারা পণ্য রফতানির জন্য বিনিয়োগে আগ্রহ কম দেখান। বাংলাদেশের রফতানি না বাড়ার পেছনে এগুলো হচ্ছে মূল কারণ। এর পাশাপাশি রফতানি বাড়াতে হলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিশ্বের যেসব দেশের রফতানি বেড়েছে সেখানে এফডিআইয়ের পরিমাণও বেশি।
দেশের মোট রফতানিতে পোশাক খাতের অবদান ৮০ শতাংশের বেশি। রফতানিতে একক একটি খাতের প্রতি এ মাত্রার নির্ভরতা অন্যান্য দেশে খুবই কম দেখা যায়। এমনকি বাংলাদেশের রফতানিতে পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্যও অনেক কম। সরকারি সংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে দেশের রফতানির গ্রাফকে ঊর্ধ্বমুখী দেখিয়ে এসেছে। যদিও বাংলাদেশের রফতানি নিয়ে প্রকাশিত সরকারি এসব পরিসংখ্যান বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত।
সর্বশেষ গত বছর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আপত্তির মুখে রফতানির পরিসংখ্যান সংশোধনে বাধ্য হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে রফতানির পরিমাণও আগের চেয়ে কমে গেছে।
আবার সরকারি পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মোট পরিমাণে বাড়তি দেখানো হলেও গত এক যুগে দেশের জিডিপির অনুপাতে রফতানির হার ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। ২০১২ সালে দেশের মোট জিডিপিতে রফতানি খাতের অবদান ছিল ২০ শতাংশ।
২০২৩ সালে এটি কমে ১৩ দশমিক ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, মূলত নীতিগত অদূরদর্শিতার কারণেই বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি।
বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ২০০৯ সালে কোরিয়ান কোম্পানি ইয়াংওয়ানের চেয়ারম্যান কিহাক সুং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে স্যামসাংকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন।
উদ্দেশ্য ছিল এখানে তাদের ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী, মোবাইল ফোন তৈরির সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু সরকার সে সময় তাদের এখানে কোনো জায়গা দেয়নি। ফলে তারা চলে গেল ভিয়েতনামে।
তিনি আরও বলেন, এখন ১৪-১৫ বছর পর এসে ভিয়েতনাম থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার শুধু স্যামসাংই রফতানি করে। এটি হচ্ছে আমাদের অদূরদর্শিতার নিদর্শন। আবার আমাদের রফতানি শুধু পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অন্য কোনো সম্ভাবনাময় খাত অনুসন্ধান করা হয়নি। এবং খাতগুলোর রফতানি বাড়ানোরও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
একটি দেশের মোট রফতানির ৮৫ শতাংশ পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হলে জনসংখ্যা যা-ই থাকুক, সে দেশে রফতানি তো বাড়বে না। ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েতনামের নানা ধরনের রফতানি পণ্য রয়েছে। ভিয়েতনামের মোট রফতানিতে পোশাক পণ্যের অবদান আমাদের চেয়ে কম। ইলেকট্রনিক পণ্যে তাদের বড় একটি রফতানি বাজার রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিতে পারেনি। আমরা রফতানির সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে পারিনি। আবার জনশক্তিকেও কাজে লাগাতে পারিনি।
আশির দশকের পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনাম, চীন, মেক্সিকো ও ভারতের মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বড় অবদান রেখেছে এফডিআই প্রবাহ। বিষয়টি রফতানি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে।
বাংলাদেশ মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে যাত্রা করে মূলত নব্বইয়ের দশকে। কিন্তু সে সময় থেকে গত তিন দশকে নতুন মূলধন নিয়ে আসা এফডিআই প্রকল্প হাতেগোনা অল্প কয়েকটি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ সময়ের মধ্যে লাফার্জহোলসিম, কোটস, ম্যারিকো, ইয়াংওয়ান, আইগ্যাজসহ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে এলেও গ্রামীণফোন ছাড়া আর কোনোটি সেভাবে উল্লেখ করার মতো ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করতে পারেনি। আর দেশে গত ছয় দশকে এফডিআই-ভিত্তিক সফল প্রকল্প হিসেবে ইউনিলিভারের নামকে সবার ওপরে রাখছেন বিদেশী বিনিয়োগ সংশ্লিষ্টরা।
বিশ্লেষকরা বলছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে এফডিআই। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতা নেই বললেই চলে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত দেশে পুঞ্জীভূত বিদেশী বিনিয়োগ স্টক রয়েছে ১ হাজার ৭৫৪ কোটি ৩০ লাখ ৮০ হাজার ডলারের। আর সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে দেশের নিট এফডিআইয়ের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ কমে ১৪৬ কোটি ৯০ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, এটা ঠিক যে রফতানিতে আমাদের যে সম্ভাবনা ছিল সেটি কাজে লাগাতে পারিনি। তবে আমাদের সম্ভাবনা এখনো আছে। সেটি কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
তৈরি পোশাক খাতের রফতানিও কয়েকটি পণ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যকরণের সম্ভাবনাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। জনসংখ্যা আমাদের বড় শক্তি। তাদের কাজে লাগাতে হলে দক্ষতা বাড়াতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এমনকি শ্রীলংকার চেয়েও আমাদের শ্রমিকদের দক্ষতা কম। আবার পোশাকের বাইরেও আরো সম্ভাবনাময় পণ্য রয়েছে। এগুলোর রফতানি বাড়াতে নীতিসহায়তা নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। পোশাক খাত যেসব সুবিধা পেয়েছে অন্যান্য খাতে রফতানি বাড়াতে হলে সেসব সুবিধা দিতে হবে।
পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি লজিস্টিকস, বন্দর সুবিধা, পরিবহন ও অবকাঠামোর মতো বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। এ জায়গাগুলোয় আমাদের ঘাটতি আছে সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে এসব বিষয়ে তুলনা করলে দেখা যায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।
তিনি বলেছেন, যে কোনো পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে প্রায় একই সময় লাগে। কিন্তু আমাদের এখানে পণ্য প্রবেশ ও বের হওয়ার লিড টাইম অন্যদের চেয়ে বেশি লেগে যায়। তখন আমাদের পণ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।
এ সমস্যা সমাধানে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে কাজ করছি। রফতানি প্রসারের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জ্বালানির নিশ্চয়তা। শিল্প খাতের জন্য আমরা এখনো জ্বালানির পর্যাপ্ত সংস্থান নিশ্চিত করতে পারিনি।
আবার এফডিআইয়েরও রফতানিতে বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আমরা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আসতে পারছি না। তবে পোশাক খাতে পণ্যের বৈচিত্রায়ণ, পশ্চাদশিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে ২০৩০ সালের আগেই আমাদের পক্ষে ১০০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।
যেসব খাতে আমাদের রফতানির ভালো সম্ভাবনা আছে এবং নীতিসহায়তা প্রয়োজন, সেগুলো নিয়ে এনবিআরের সঙ্গে কাজ চলছে। চামড়া খাতেও রফতানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। আমরা আশাবাদী সামনে আমাদের রফতানির পরিমাণ আরো বাড়বে।
সূত্র: বণিক বার্তা

-20250202060928.webp)
-20250202070418.webp)
-20250202064748.webp)
-20250202055759.webp)

-20250201152103.webp)
-20250201124257.webp)


-20250202095549.webp)










-20250202083427.webp)




-20250128063132.jpg)





-20250129052907.jpg)

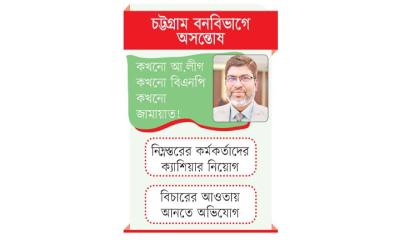





আপনার মতামত লিখুন :