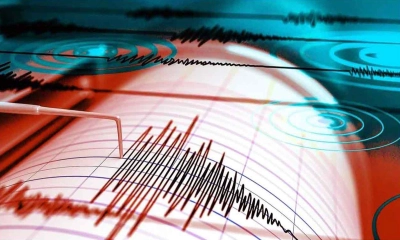বাংলাদেশ ক্রমশ ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যেই ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূকম্পনে কেঁপে উঠছে দেশ। যদিও এসব ভূমিকম্পে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না, তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে বড় মাত্রার ভূমিকম্প ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, একের পর এক স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলছে। পূর্বাভাসের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগও বাড়ছে।
চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম সাত দিনের মধ্যেই দেশে দুবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জানুয়ারি সকালে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্প ছিল তুলনামূলক শক্তিশালী, আর ৩ জানুয়ারির ভূমিকম্প ছিল মাঝারি মাত্রার। তবে এই দুটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের বাইরে। ৭ জানুয়ারির ভূমিকম্পের উৎসস্থল চীনের ঝিজিয়াং অঞ্চল, আর ৩ জানুয়ারির ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মিয়ানমারের হোমালিন এলাকা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎপত্তিস্থল দেশের বাইরে হলেও এক সপ্তাহে দেশে দুবার ভূমিকম্প অনুভূত হওয়া বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাপক ভূমিকম্পের ঝুঁকির মুখোমুখি। ঘনবসতি, পুরোনো অবকাঠামো এবং দুর্বল বিল্ডিং কোড এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।
নেপাল, ভারত, ভুটান ও চীনেও সাম্প্রতিক ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে, যা ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগের আন্তঃদেশীয় মাত্রা তুলে ধরে। ইতিহাসে দেখা গেছে, ১৮৬৯ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৭-এর ওপরে পাঁচটি বড় ভূমিকম্প হয়েছে। এরপর থেকে উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প কিছুটা স্তিমিত থাকলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি বড় ভূমিকম্পের আগে একটি নীরব সতর্কতা হতে পারে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমিকম্পের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালের রেকর্ড অনুযায়ী, ৬০টি ভূমিকম্পের মধ্যে তিনটি ছিল ৪ মাত্রার ওপরে এবং ৩১টি ছিল ৩ থেকে ৪ মাত্রার মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি, শহর এলাকায় এর বিস্তৃতি ও দুর্বল অবকাঠামো বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।
বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ ২০টি শহরের তালিকায় ঢাকার নাম রয়েছে। ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধস দুর্বল নির্মাণশৈলীর ভয়াবহ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১৮ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, পল্লবী, রামপুরা, মতিঝিল ও খিলগাঁও এলাকার অনেক ভবন কাঠামোগত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ।
চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের জৈন্তাপুর অঞ্চলকে চরম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
২০২৪ সালের মার্চে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) বাংলাদেশে আন্তঃদেশীয় ভূমিকম্প ঝুঁকি মূল্যায়ন চালু করেছে। জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যালয় (ইউএনডিআরআর) ও গ্লোবাল ভূমিকম্প মডেল (জিইএম) ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
মূল মূল্যায়নে যে প্রধান ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে:—
ভঙ্গুর অবকাঠামো: হাসপাতাল, জরুরি সেবা কেন্দ্র ও সরকারি ভবন ভূমিকম্প সহনশীল নয়, এগুলোর দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।
নগর পরিকল্পনার ঘাটতি: দুর্বল বিল্ডিং কোড ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে।
জনসচেতনার অভাব: অনেক নাগরিক ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও নিরাপত্তাবিধানের বিষয়ে সচেতন নন।
বিশেষজ্ঞরা ঝুঁকি হ্রাসে সমন্বিত কৌশলের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাদের সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে— ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা, ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসামরিক-সামরিক সমন্বয় বৃদ্ধি।
বাংলাদেশ যদি আন্তঃদেশীয় মূল্যায়নের সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে, তাহলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।