সম্প্রতি মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে ঘটে যাওয়া শক্তিশালী ভূমিকম্প আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে, এই ভূমিকম্পের ফলে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমেছে কি না।
ভূতাত্ত্বিক গবেষকরা বলছেন, একটি অঞ্চলে ভূমিকম্প হলেও নিকটবর্তী অন্য অঞ্চলে চাপ তৈরি হতে পারে, যা আরও বড় ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে। তাই আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। বরং এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করতে হবে।
বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা ভূমিকম্পের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই এলাকাগুলোর ভূগর্ভস্থ স্তরে বেশ কয়েকটি সক্রিয় ফাটল রয়েছে, যা যেকোনো সময় শক্তিশালী ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।
বিশেষ করে, ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের কারণে বাংলাদেশের ভূত্বকের নিচে ব্যাপক চাপ সঞ্চিত হচ্ছে, যা একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হতে পারে।
চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাছে অবস্থান করা মিয়ানমারের রাখাইন ফ্রন্ট এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেঘালয় ভূগর্ভস্থ ফাটল অঞ্চলগুলো ভূমিকম্পের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে।
এই এলাকাগুলোতে অতীতে একাধিক মাঝারি ও শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত বহন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ৮ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প ঘটে, তাহলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
বাংলাদেশের ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে। বিশেষ করে, ঢাকার মতো মহানগরীগুলোতে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকম্প প্রতিরোধী নীতিমালা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না।
অধিকাংশ পুরোনো ভবন ও অপরিকল্পিত বহুতল ভবন ভূমিকম্প প্রতিরোধী নীতির বাইরে নির্মিত, যা বড় ভূমিকম্পের সময় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। শুধু তাই নয়, ঢাকার মাটির গঠনও ভূমিকম্পের সময় কম্পন বাড়াতে পারে, যা ভবন ধসে পড়ার ঝুঁকি অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে।
বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, যদি এই ভূমিকম্পের প্রস্তুতি নেওয়া না হয়, তাহলে যেকোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্পে বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।
বড় ভূমিকম্প ঘটলে যা হতে পারে
বাংলাদেশে যদি ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প ঘটে, তাহলে পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় বহুতল ভবনের অপরিকল্পিত নির্মাণ, দুর্বল অবকাঠামো, সরু গলি, অপর্যাপ্ত উদ্ধারকর্মী ও দুর্বল জরুরি সেবা ব্যবস্থায় মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, বড় ভূমিকম্প হলে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতেও তা বড় ধাক্কা দেবে।
ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়ার সংখ্যা এত বেশি হতে পারে যে, উদ্ধার কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়বে। ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থার সক্ষমতা এই মাত্রার বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ধসেপড়া ভবনের নিচে কয়েক দিন আটকে থাকার কারণে অক্সিজেনের অভাব, খাবার ও পানির সংকটে প্রাণহানি ঘটাতে পারে।
এছাড়া, ভূমিকম্পের পর অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও অত্যন্ত বেশি। ঢাকার পুরান অংশে এবং অন্যান্য এলাকায় গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক তার ও রাসায়নিক গুদামগুলো ভূমিকম্পের সময় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যা ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমিকম্পের পর অগ্নিকাণ্ড যদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপর্যয় ডেকে আনবে।
যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে, মূল সড়কগুলো ধসে গিয়ে হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে সুপেয় পানির সংকট, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি না নেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প হলে এর প্রভাব শুধু জীবনহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এটি অর্থনীতি, অবকাঠামো, পরিবেশ এবং সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে ধ্বংসাত্মক অবস্থায় নিয়ে যাবে।
ভূমিকম্প-পরবর্তী প্রস্তুতি
সরকারিভাবে কিছু পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের অভাব প্রকট। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিলেও তা অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ পরিকল্পনা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, যার ফলে বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি গড়ে ওঠে না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে মানা জরুরি, কিন্তু বাংলাদেশে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণে দক্ষ প্রকৌশলী ও মানসম্পন্ন নির্মাণসামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।
স্থানীয় সরকার ও রাজউকের নজরদারির অভাবে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিতভাবে বহুতল ভবন গড়ে উঠছে, যা বড় ধরনের ভূমিকম্পে ধ্বংসযজ্ঞের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে।
উদ্ধার কার্যক্রমেও বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে জীবিতদের উদ্ধার করতে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তা অপ্রতুল। উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত রেসকিউ রোবট, হেভি-লিফট ক্রেন, থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ও স্নিফার ডগের সংখ্যা খুবই সীমিত।
অধিকাংশ উদ্ধারকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ পুরোনো এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো- সাধারণ জনগণের ভূমিকম্প সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব। বেশিরভাগ মানুষ জানেন না ভূমিকম্প চলাকালীন কী করতে হবে কিংবা কোথায় আশ্রয় নিতে হবে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ও আবাসিক এলাকায় ভূমিকম্প মোকাবিলার মহড়া (ড্রিল) অত্যন্ত কম হয়, ফলে বাস্তব পরিস্থিতিতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে।
এই বাস্তবতায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস করতে কেবল পরিকল্পনা করলেই হবে না, বরং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উদ্ধার সরঞ্জাম বাড়ানো, প্রশিক্ষিত কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ভবন নির্মাণে বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।
ভূমিকম্প বাজেট বাড়ানো জরুরি
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। বর্তমান বাজেট সীমিত হওয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সুসজ্জিত করতে হবে। উন্নত উদ্ধার সরঞ্জাম, ভূমিকম্প পূর্বাভাসের জন্য গবেষণাগার, ভূকম্পন পরিমাপক স্টেশন ও জরুরি পদক্ষেপের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে বড় আকারের বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভূমিকম্প প্রতিরোধী অবকাঠামো গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। যেসব শহর ভূমিকম্পপ্রবণ, সেখানে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আধুনিক বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
স্কুল, হাসপাতাল, সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং জনবহুল স্থাপনাগুলো ভূমিকম্প সহনশীল করে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি, পুরোনো ভবনগুলোর ভূমিকম্প প্রতিরোধী সংস্কার জরুরি। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বড় আকারে বাড়াতে হবে।
গবেষণার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিরূপণের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করতে হবে।
ভূকম্পন পর্যবেক্ষণের জন্য আরও ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভূমিকম্পবিষয়ক গবেষণা তহবিল বৃদ্ধি এবং ভূমিকম্পের প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি।
বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল যেন যথাযথভাবে ব্যয় হয় এবং কোনো ধরনের অনিয়ম না ঘটে, তা কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। একমাত্র সঠিক পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম হতে পারে।
পূর্বপ্রস্তুতি ও জনসচেতনতা
জনসচেতনতা বৃদ্ধি ভূমিকম্প মোকাবিলার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। ভূমিকম্পের সময় মানুষ কীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে কীভাবে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে হবে- এ বিষয়ে সবার মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত ভূমিকম্প প্রশিক্ষণ চালু করা দরকার।
প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প মোকাবিলার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকম্পের সময় সঠিক প্রতিক্রিয়া প্রদানের কৌশল শেখানো দরকার, যেমন- টেবিলের নিচে আশ্রয় নেওয়া, মাথা ও ঘাড় সুরক্ষিত রাখা এবং ভূ-কম্পন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ অবস্থানে থাকা।
কর্মক্ষেত্রে ভূমিকম্প প্রশিক্ষণের ওপরও জোর দিতে হবে। অফিস ভবনগুলোর জরুরি বহির্গমন পথ চিহ্নিত করা, ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করা এবং কর্মীদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শপিং মলগুলোর জন্য ভূমিকম্প মহড়া (ড্রিল) চালু করতে হবে, যাতে কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে আসতে পারে।
আবাসিক এলাকাগুলোতেও জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্থানীয় প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক এলাকায় ভূমিকম্পকালীন নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা, উদ্ধার সরঞ্জাম মজুত রাখা এবং জনগণকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, ভূমিকম্প মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারণা বাড়াতে হবে। ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরা নিরাপদ থাকার পাশাপাশি অন্যদেরও সহায়তা করতে পারে।
বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে, কিন্তু প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে বড় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। পরিকল্পিত নগরায়ণ, আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আজই প্রস্তুতি নিতে হবে, নতুবা দুঃসহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
লেখক: সাংবাদিক, কলাম লেখক ও সমাজ গবেষক মহাসচিব: কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ।
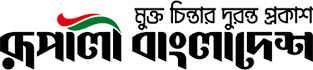


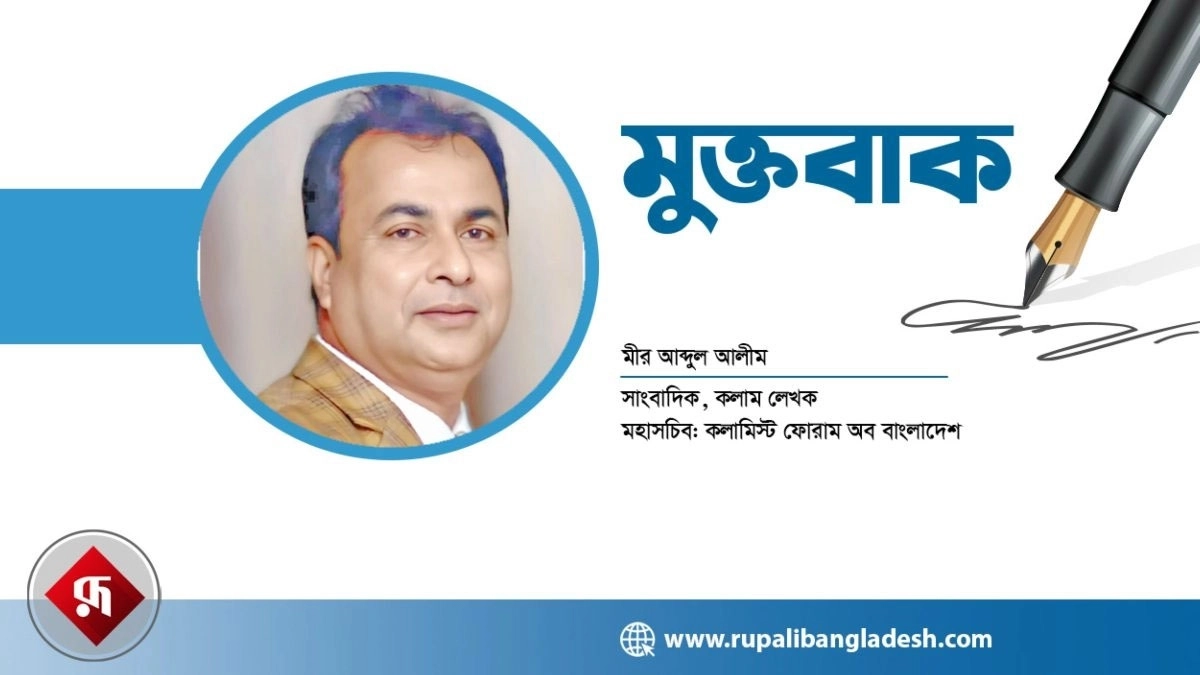




-20250415074300.webp)
-20250413175442.webp)

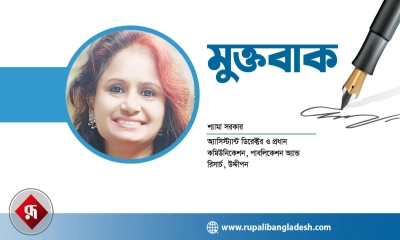
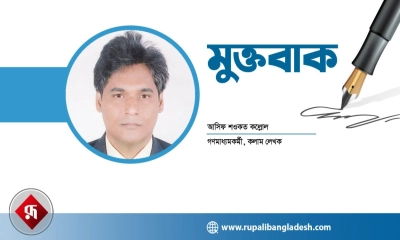















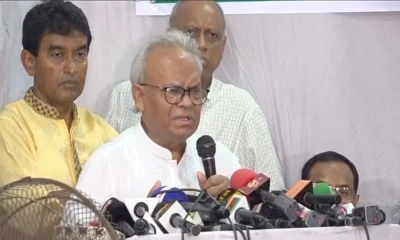




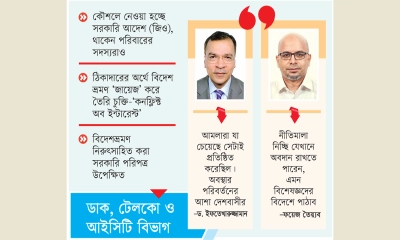

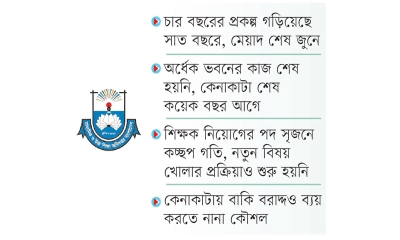








আপনার মতামত লিখুন :