উন্নয়ন হলো একটি তন্ত্র বা পদ্ধতি যা একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবেশগত পরিশুদ্ধিসহ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের ইতিবাচক পরিবর্তনের পরিচায়ক। যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বাধা বা অন্তরায় তা হলো ‘অ’ সূচক শব্দের সমষ্টি। এই `অ` এর বিষয়টি আমরা প্রারম্ভেই পরিষ্কার করে নিতে পারি।
১. অজ্ঞতা, ২. অশিক্ষা, ৩. অলসতা, ৪. অদক্ষতা, ৫. অসচেতনতা, ৬. অযোগ্যতা, ৭. অস্বচ্ছতা, ৮. অসততা, ৯. অসহিষ্ণুতা, ১০. অমানবিকতা, ১১. অনৈতিকতা, ১২. অদূরদর্শীতা, ১৩. অপরাজনীতি, ১৪. অসীম অপচার (দুর্নীতি) ১৫. অপসংস্কৃতি, ১৬. অপপরিকল্পনা, সর্বোপরি ১৭. অব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
১.অজ্ঞতা
অজ্ঞতা মানে মূর্খতা, হীনবোধ বা হীনজ্ঞান। আরো সহজ করে বললে বলা যায় কোনো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকা বা জ্ঞান শুন্যের কোঠায়। এই অজ্ঞতা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অর্থাৎ শ্রেণি নির্বিশেষে কমবেশি বিরাজমান । অজ্ঞতা থেকেই অন্ধকারের সৃষ্টি। সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো অজ্ঞতা। কেননা, কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে উন্নয়নের ন্যূনতম কোনো সম্ভাবনাও কাজ করে না। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। এর সমার্থক শব্দসমূহের মধ্যে রয়েছে বিস্তৃতি, প্রসারণ, বিবর্তন, বৃদ্ধি, প্রগতি, অগ্রগতি, উত্তরণ, বিকাশ প্রভৃতি। সাধারণভাবে বলা যায় উন্নয়ন হলো কোনো অগ্রগতি বা কোনো অগ্রস্রিয়মাণ অবস্থা যা কোনো কিছুর বৃদ্ধি বা ব্যাপকতার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়। অভিধানে উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে “A process of unfolding, maturing and evolving" অর্থাৎ উন্নয়ন হলো উদ্ঘাটন, পরিপক্বতা এবং বিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। উন্নয়নের এ অর্থ ও ধারণা মানবসমাজের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এক কথায় বলতে পারি উন্নয়ন হচ্ছে চলমান অবস্থা বা স্তর থেকে আরো উন্নত এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বা স্তরে উত্তরণ। একটি রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে না পারে তবে তারা অজ্ঞতার বেড়াজালে আটকা পড়ে। এই অজ্ঞতার কারণে নাগরিক তার রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। কারণ, নাগরিক তার উচিত-অনুচিত এবং করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। যার প্রভাব পড়ে সরাসরি উন্নয়নে। অজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে না। তার ভেতর রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতা এবং অবৈধ পন্থায় নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার মানসিকতা তৈরি হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে অসৎ ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। তাই অজ্ঞতা উন্নয়নের একটি বড়ো অন্তরায় বা বাধা। এই অচলায়তন ভাঙার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং আত্মসচেতনতার উদ্বোধন করা। তবেই রাষ্ট্রের উন্নয়নের অভিযাত্রায় অজ্ঞতা আর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না।
২.অশিক্ষা
যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তরিত হয়। দেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তরিত হলে উন্নয়নের স্বয়ংক্রিয় ধারা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে সীমাহীন উদ্ভাবনী শক্তি এবং অসংখ্য গুণাবলি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। শিক্ষার কাজ হলো সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ ঘটানো ও উদ্ভাবনী শক্তি উজ্জীবিত করা এবং উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দান করে আর এ জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টির সেরা বলেই মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছে, পেরেছে নিজের মতো কাজে লাগাতে । জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে এবং এভাবেই সমাজ গড়ে উঠছে এবং এগিয়ে চলছে সভ্যতা। শিক্ষা মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করে এবং মূল্যবোধ সমৃদ্ধ করে যা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য অপরিহার্য। কাজেই একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য বলা হয় ‘শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড`। আর এর চালিকাশক্তি হিসেবে শিক্ষকই হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। শিক্ষক যেহেতু মেরুদণ্ড সেহেতু শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মানের জায়গাটিও সুসংহত করা জরুরি। শিক্ষারই বিপরীত ধারণাটি হলো অশিক্ষা অর্থাৎ যথাযথ শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষা যদি যথাযথ না হয় তাহলে অশিক্ষা রূপ নেয় সকল প্রতিবন্ধকতার। অজ্ঞতার কথা বলছিলাম। এই অশিক্ষা থেকেই অজ্ঞতার জন্ম। কেননা প্রকৃত শিক্ষা যেমন সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে তেমনই অশিক্ষা ঠেলে দিতে পারে বহুমাত্রিক ব্যর্থতার দিকে। সামগ্রিক উন্নয়ন-ধারণায় অশিক্ষা একটি বড় বাধা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি বেগবান করা অসম্ভব। তবে মানুষকে তিনি নিছক পুঁজি হিসেবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন অশিক্ষার রাহুমুক্ত হয়ে মানুষ সর্বাঙ্গীণ মানবকল্যাণের ভেতর দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করুক। অশিক্ষা মানুষের উৎপাদন কলাকৌশল অর্জন ও উন্নয়নের সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি পালনে প্রতি পদে বাধা প্ৰদান করে। জনগণকে উন্নত জীবনযাপনে উৎসাহী করতে শিক্ষার প্রয়োজন। একমাত্র শিক্ষাই পারে তাদের প্রকৃত জীবনবোধ জাগ্রত করতে। শিক্ষা মানুষকে সুসজ্জিত, আলোকিত এবং হৃদয়ের মাঝে সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলোকে প্রস্ফুটিত করে। সুতরাং আমাদের সার্বিক উন্নয়নে অশিক্ষার বলয় থেকে বের হয়ে সৎ চিন্তা, সৎ কর্মে উদ্দীপ্ত হয়ে যথাযথ কর্মকৌশল, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের গুণে গুণান্বিত হবো-এই অঙ্গীকার জরুরি।
৩.অলসতা
পৃথিবীর সব অঞ্চল বা দেশে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি পরিবারেই আলস্য বা অলসতায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায়। তারা বহুলাংশেই চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যের সঙ্গে সামাজিক বা আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে তুললেও সর্ব ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অলসতায় জর্জরিত ব্যক্তি অন্য মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদাকে বুঝতে পারে না, হতে পারে না উন্নয়নের অংশীজন। একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে অলসতার কোনো স্থান নেই। কেননা আলস্যের কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী ও ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ব্যাহত হচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র। তবে আরেক দিক বিবেচনায় মনে হয় আমরা আসলে অলস নই, আমরা অনুপ্রাণিত নই বলেই আলস্য আমাদের ওপর ক্রমাগত ভর করে চলেছে। প্রতিদিন একই কাজ করতে করতে ক্রমশ নিস্তেজ হয় যাই। জীবনে সজীবতা নেই বলে পেশাজীবনে যেমন আলস্যতা পরিলক্ষিত হয় তেমনি দিন দিন ব্যক্তিজীবন হয়ে ওঠে বর্ণহীন। যে কোনো জাতির উন্নয়ন হলো একটি অব্যাহত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে, সম্পদের সুষম বণ্টনের দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলমানবিক চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে জনগণের পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা বাছাই করার ক্ষমতা বাড়বে। সুতরাং এই সামগ্রিক কার্যক্রমে আলস্যের কোনো স্থান নেই। আলস্যের আশ্রয়ে এ সকল কাজ কোনো ভাবেই পূর্ণতা পাবে না। সুতরাং রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে আমরা আলস্য পরিহার করে একটি উন্নত ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়বো-এই হোক আমাদের দৃঢ় প্রতীতি ।
৪.অদক্ষতা
অদক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। অদক্ষ জনগোষ্ঠী কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না। অগ্রপ্রিয়মাণ অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণের মধ্যে সর্বাগ্রে দক্ষতার ঘাটতির বিষয়টি বিবেচ্য। উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সবার আগে দরকার মানবসম্পদের উন্নয়ন। মানসম্মত শিক্ষা তথা কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাই পারে এর নিশ্চয়তা দিতে। এটি দক্ষতা উন্নয়নের কার্যকর উপায়। দক্ষতা থাকলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী আয়-উপার্জন এবং শ্রমের বিনিময়ে ভালো অর্থপ্রাপ্তিরও নিশ্চয়তা মেলে। এর ফলে পরিবার ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটে। আর এর সার্বিক প্রভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির দিকে অগ্রগামী হয় । অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। সামাজিক জীবনমানের পাশাপাশি দেশের উন্নতির জন্য দরকার ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষার প্রসার। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। অবশ্য তা বাস্তবায়নে শিক্ষা পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। তবেই অদক্ষতা কোনোভাবেই উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অপরদিকে সামগ্রিক পর্যায়ে কর্মক্ষম ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। অদক্ষতার বেড়াজাল থেকে জনগোষ্ঠীকে দক্ষতার পতাকাতলে আনতে না পারলে কখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। সবার আগে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু তাই নয় এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগও বর্ধিত করতে হবে। অদক্ষতা কখনো একটি রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতায় ভূমিকা রাখতে পারে না, এতে করে প্রবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে আটকে থাকে। এ অবস্থায় আমাদের উন্নয়নশীল দেশের ধাপ পেরিয়ে উন্নত দেশে পৌঁছানোর স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সুতরাং আমাদের উন্নয়নের পথে অদক্ষতা যেন কোনো মতেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আর এ কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কর্মমুখী দক্ষতা, প্রশিক্ষণের মান এবং উৎপাদনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিকল্প নেই ।
৫.অসচেতনতা
উন্নয়নের সামষ্টিক ধারণায় অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সচেতনতা বা সতর্কতা। অসচেতনতা এর বিপরীত ধারণা অর্থাৎ সতর্কতার অভাব বা উদাসীন মনোভাব পোষণ করা। যে কোনো বিষয়ে সচেতন না হলে আমরা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে শতভাগ ব্যর্থ হবো এতে কোনো দ্বিধা নেই। কেননা কোনো অসচেতন বা উদাসীন ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা অসম্ভব। অসচেতনতা রাষ্ট্রীয় জীবনে আনতে পারে হাজারও সমস্যা আবার একটু সচেতনতা আনতে পারে সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। এমন কিছু ছোটোখাটো অসচেতনতা আছে যা থেকে আমরা খুব সহজেই সচেতন হতে পারি এর জন্য তেমন কোনো শিক্ষারও প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার একটু সতর্ক দৃষ্টি। জীবনের পথ চলতে গিয়ে প্রতিদিনের জীবনযাপনে আমরা নানা বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন হই। কিছু সমস্যা সহজেই সমাধানযোগ্য, আবার কিছু সমস্যা এত জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে এর প্রতিকার তো দূরের কথা উপরন্তু তা আমাদের জীবনে ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনে। অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই এ সব সমস্যা থকে খুব সহজেই দূরে থাকতে পারি যা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে মুক্ত করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারি। রাষ্ট্র সাধারণ নাগরিকের মৌলমানবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, বাসস্থান সমস্যার সমাধান, জনগণের মুক্ত ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মানুষকে নিরাপদ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমরা যদি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সচেতন না হই, প্রতি পদে পদে অসচেতনতার পরিচয় দেই তাহলে প্রশ্ন ওঠে আমরা উন্নয়নের এ অব্যাহত ধারা কীভাবে টিকিয়ে রাখবো? উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের সার্বিক বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমাদের অসচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো আমাদের অশিক্ষা ও অলসতা। সুতরাং আমাদের মূর্খতা ও আলস্য পরিহার করে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নয়নের সহযাত্রী হিসেবে পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। তবেই সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে।
৬.অযোগ্যতা
‘অযোগ্যতা` শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যর্থ মানুষের অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই অযোগ্যতা মানুষটির শিক্ষা কিংবা কর্মক্ষেত্র, দুটো দিককেই সামনে নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক নাটকে এক চরিত্রের মুখ দিয়ে ‘অযোগ্যতা` শব্দটির সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে : ‘অযোগ্যতা হচ্ছে শূন্য পেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।` কথাটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। শূন্য পেয়ালা তো কৃপা দিয়েই পূর্ণ করে তুলতে হয়। কৃপা যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে সেখানে কর্মশক্তি আড়ালে পড়ে যায়। কর্মহীন মানুষ কী করে সাফল্যের নাগাল পাবে? আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে এখন যতসব অযোগ্য মানুষের বৃথা আস্ফালন। প্রকৃত অর্থেই যোগ্য মানুষের বড়ো অভাব । তবে এটাও ঠিক, কাউকে অযোগ্য আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। বরং তার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ফলে পরিবার তথা সমাজ থেকে ছিটকে পড়া ঐ ব্যক্তিটি খুঁজে পাবে ঘুরে দাঁড়াবার অবলম্বন। এরিস্টটল বলেছেন, যোগ্যতা রাতারাতি কখনোই হয় না, এটা হলো একটা অভ্যাস যা তৈরি করে নিতে হয়। মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড বলেছেন, ‘যোগ্যতা হলো তা যা একজন ব্যক্তিকে কেউ না থাকলেও কোনো কিছু সঠিকভাবে করার শক্তি জোগায়।` তবে অযোগ্য মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র দ্রুত পিছিয়ে পড়ে। ফলে তেমন পরিস্থিতি উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ।
৭.অস্বচ্ছতা
ইংরেজিতে ‘অস্বচ্ছতা` শব্দটিকে বলা হয় lack of transparency। ব্যক্তি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অস্বচ্ছতা নানা ধরনের জটিলতা তৈরি করতে পারে। একজন ব্যক্তি যখন পারিবারিক পরিমণ্ডলে আচার- আচরণে ধোঁয়াশা তৈরি চলেন, তখন নানারকম বিপত্তি তৈরি হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি তার পরিবারে যথাযথ গুরুত্ব পান না। তাকে বাদ দিয়েই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কথা একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিবেচ্য, তা ‘রাষ্ট্র` কিংবা `সমাজ`-এর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যদি যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদাররা কোনো হিসাবের তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো খরচ করতে থাকেন, তাহলে কিছুদিন পরই পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হতে বাধ্য। আর এই সন্দেহের মাত্রা যত বাড়তে থাকবে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ততই বাড়তে থাকবে অসন্তোষ। এমন একটা সময় আসবে যখন ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হবে। আমরা যদি দেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে নানামাত্রিক অস্বচ্ছতা। ফলে সম্পর্কের এই অস্বচ্ছতা দুটি রাষ্ট্রকে সংঘাতের পথে নিয়ে যায়। ২০০৩ সালের মার্চে ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ ইরাকের পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বচ্ছ ধারণারই ভয়াবহ ফল। আর সাম্প্রতিক কালে পদ্মা সেতুর ঋণ প্রকল্প নিয়ে বিশ্ব ব্যাংক যে lack of transparency-এর অভিযোগ তুলেছিল পরবর্তী সময়ে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে বিশ্ব ব্যাংকের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর অন্যদিকে পদ্মা সেতুর সফল বাস্তবায়ন বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে উজ্জ্বল করেছে। তবে এ কথাও সত্য, অস্বচ্ছতা যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেই বিশেষ অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক ।
৮.অসততা
অভিধান বলছে ‘অসততা`র অর্থ সততা বা সাধুতার অভাব। মিথ্যাচারিতাকেও অসততা বলা যায়। অসৎ চিন্তাও অসততার সমার্থক। মহানবি (সা.) তাঁর শৈশবেই সত্যবাদিতা তথা সততার জন্য ‘আল আমিন’ খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। ভিন্ন গোত্র কিংবা ধর্মের লোকেরাও তাঁর কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন এই বিশ্বাসে যে, মুহম্মদ (সা.) আমানতের খেয়ানত করবেন না। অসততা একজন মানুষকে নিম্ন স্তরে নিয়ে যায়। অবিশ্বস্ত মানুষ সমাজে কখনোই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসক ও লেখক স্পেন্সার জনসন একটা চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় : ‘নিজের কাছে সত্য বলা হলো আন্তরিকতা আর অন্যের কাছে সত্য বলা হলো সততা।` বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মতে, ‘সততা হলো সেরা নীতি। আমি যদি আমার সম্মান হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবো।` অসততা সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলতা তৈরি করে। মাঝেমধ্যেই আমরা পত্রপত্রিকায় দেখি, অমুক ঋণখেলাপি অমুক ব্যাংকের হাজার কোটি টাকা মেরে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এমন তথাকথিত ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতির সংখ্যা দেশে দিনদিনই বাড়ছে। এসব ঘটনা আমাদের সমাজকে নিরন্তর কলুষিত করছে। সততা একজন মানুষের মধ্যে ইতিবাচক শক্তির জন্ম দেয়। আর এই ইতিবাচক শক্তি কাজে লাগিয়ে একজন ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রসত্তাও কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সাক্ষাৎ পায়। সততা প্রসঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আরও একটি কথা বলেছেন : ‘কোনো উত্তরাধিকারই সততার মতো সমৃদ্ধ নয়।` তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ব্যক্তি তথা সমাজ উন্নয়নে অসততা প্রধান প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়।
৯.অসহিষ্ণুতা
উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ। সহিষ্ণুতার অভাবই অসহিষ্ণুতা। এটি মানবচরিত্রের একটি নর্থক বৈশিষ্ট্য। কথায় আছে, `যে সহে সে রহে` যুগে যুগে সেসব মহাপুরুষ ও যুগন্ধর ব্যক্তি দেশ-কাল-সমাজ ও মানবসমাজের জন্য বড়ো কিছু দিয়ে গেছেন তারা ছিলেন সহিষ্ণু। উন্নয়নের জন্য সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। আর অসহিষ্ণুতা উন্নয়নের নিশ্চিতভাবে অন্তরায়। যেকোনো উন্নয়ন কাজ শুরু হলে তার সঙ্গে জড়িত থাকে নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। যেমন উন্নয়নকর্ম সাধিত এলাকার লোকজন যদি উন্নয়নকর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা না দেখায় তা হলে তা বিশেষভাবে অন্তরায় হতে বাধ্য। উন্নয়ন কাজ শুরু হলে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় লোকজনের সাময়িক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যেমন- মেট্রোরেলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার দীর্ঘ সময় অন্যান্য এলাকার মতো মিরপুরবাসী বেশ দুর্ভোগের স্বীকার হয়েছেন। তাদেরকে বিকল্প সরু পথ ব্যবহারের কারণে যানজট ও ভিড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এতে জনজীবন অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষ বিরক্ত হলেও ভেবেছে মেট্রোরেলের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে তাদের এই দুর্ভোগ থাকবে না। তারা যদি তখন অসহিষ্ণু হয়ে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হতো তাহলে এটি কোনো মতেই উন্নয়নে সহায়ক হতো না। তখন দেখা গেছে পত্র-পত্রিকাসমূহ কমবেশি ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে উন্নয়নের সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকল্প কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরও ছিল। কারণ দেখা যায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছিল। তখন তারা সেই অতিরিক্ত সময়টুকু ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে উন্নয়ন কাজটিকে সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট লোকজন নয়, উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে দেশবাসীর ইতিবাচক ধারণা থাকা দরকার। অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও গোষ্ঠী বিশেষের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উন্নয়নের বিরোধিতা করা হয়। সাধারণ মানুষ ভাল করে না জেনেই অনেক সময় হুজুগে মেতে ওঠে। এর কারণ মূলত দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অদূরদর্শী মনোভাব। তাই অসহিষ্ণুতার কারণে অনেক সময় উন্নয়ন দীর্ঘায়িত হয়, ব্যাহত হয় এবং সর্বোপরি ভূলুণ্ঠিত হয়।।
১০.অমানবিকতা
ইংরেজিতে শব্দটিকে বলা হয় inhumanity। প্রতিদিন চোখ মেললেই আমরা দেখি নানা অমানবিক কর্মকাণ্ড—হত্যা, ধর্ষণ, পাশবিক নির্যাতন ইত্যাদি। এটা ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন সত্য তেমনি সত্য জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। আমাদের পাশের দেশ মিয়ানমারে ক`বছর আগে সরকারি সেনাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ধর্মীয় লেবাসধারীরা যেভাবে আরাকানের নিরীহ রোহিঙ্গাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায় তাতে বিশ্ববিবেক মুষড়ে পড়ে। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন-কোনোটাই বাদ রাখেনি মিয়ানমারের শাসকচক্র! রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করেও যেন তাদের জেদ মেটেনি। রোহিঙ্গারা যেন কখনোই স্বভূমিতে ফিরে যেতে না পারে, তার জন্য প্রতিনিয়ত আঁটছে নানা অপকৌশল । মানননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ১০/১২ লাখ নির্যাতিত-নিপীড়িত অসহায় রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে তাৎক্ষণিক আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা শুধু কেবল তাঁকে নয় গোটা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি সেনাদের যে অমানবিক আচরণ দেখি, তাতে সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই মর্মাহত হন, ক্ষুব্ধ হন। সম্প্রতি ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া যেভাবে অন্যায় আক্রমণ শুরু করেছে, তাতে সেখানে শুরু হয়েছে মানবিক বিপর্যয়। এই অমানবিকতা তথা আগ্রাসি যুদ্ধ বিশ্বকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে, এটা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। কেউ কেউ বলছেন, রাশিয়ার এই আগ্রাসন গোটা বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কি না সেটাই বা কে জানে!
১১.অনৈতিকতা
নৈতিকতা মানবচরিত্রের বড়ো শক্তি। নৈতিক শক্তির বলেই একজন মানুষ ও একটি জাতি এগিয়ে যায় সাকল্যের স্বর্ণদুয়ারে । নৈতিক শক্তির আধার হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল আস্থা। মিথ্যাকে আশ্রয় করে নৈতিক শক্তি জাগ্রত থাকতে পারে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমপর্বে পাকিস্তানি বাহিনী বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কেন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল? কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা বেসামরিক ও সাধারণ লোকজনের ওপর নিপীড়ন করেছে, গণহত্যা-নির্যাতন করেছে। কলে যুদ্ধাকালীন তাদের এক প্রকার নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। অনৈতিকতা ব্যক্তির মানসিক শক্তিকে বিপন্ন ও দূর্বল করে দেয়। উন্নয়ন কাজ যখন সম্পন্ন হয়। তখন তার সঙ্গে জড়িত থাকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা যদি মনে করে এটি জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের তাহলে সে কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবেই। কিন্তু তার বিপরীত চিত্রই ভয়াবহ। এ কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি আর্থিক প্রলোভনে পড়ে উন্নয়ন কাজের নানা স্তরে আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করেন, এ প্রকল্প পাশের সঙ্গে জড়িতরা কাজের গুণগত মান নিম্ন হওয়া সত্ত্বেও তা অনুমোদন করেন তাহলে তা কোনো মতেই উন্নয়ন কাজের সহায়ক হতে পারে না। তারা যদি একবার ভাবেন এ উন্নয়ন কাজটি দেশের মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে, বর্তমান ও উত্তরপ্রজন্ম এ সুফল ভোগ করবে, এ কাজের অর্থসংস্থান হয়েছে দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের কষ্টের ট্যাক্সের টাকায়, তাহলে তিনি উপরিউক্ত অনৈতিকতার দ্বারস্থ হতে পারেন না। বিবেকের দংশন থাকলেও তারা অনৈতিকতা পরিহার করতে বাধ্য। কিন্তু এমন কম প্রকল্প ও উন্নয়ন কাজ পাওয়া যাবে যেখানে অনৈতিকতার শিকার হয়নি। মূলত যে কোনো উন্নয়ন কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নৈতিকতাকে নিশ্চিত করা সমীচীন। নয়তো অনৈতিকতার ছোবলে উন্নয়ন কাজ বিলম্বিত হবে, বাধাপ্রাপ্ত হবে উন্নয়নের সুস্থ প্রবাহ
১২.অদূরদর্শিতা
অদূরদর্শিতা একটি নেতিবাচক শব্দ। যে কোনো দেশের উন্নয়নের সুফলের জন্য তা চরম প্রতিবন্ধক। যে কোনো কাজের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতা। দেশের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে সে কাজের জন্য দরকার দূরদর্শিতা। হয়তো কোনো সড়কের ওপর খাল বা নালার জন্য একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সেই ব্রিজের নিচ দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারে না। ফলে আশেপাশের এলাকার লোকজন খাল পারাপারে ব্যর্থ হয়। এটি এলাকাবাসীর মধ্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ফলে এই ব্রিজ নির্মাণ করে যে উন্নয়ন করা হয়েছিল তা উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে দেখা দিলো। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পাতায় এমন সংবাদ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা যেতে পারে। একজন বিজ্ঞানী মুরগি পালতেন। মুরগি বাসা থেকে বড় খোপ দিয়ে আসা-যাওয়া করে। মুরগিটি বাচ্চা দিল। এবার বিজ্ঞানী ভাবলেন এখন বাচ্চাগুলি কোন্ দিক দিয়ে আসা-যাওয়া করবে? তখন তিনি বড় খোপের পাশে ছোট ছোট কয়েকটি খোপ কাটলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! বিজ্ঞানী দেখলেন বাচ্চাগুলি ছোট খোপ দিয়ে বের হচ্ছে না। এভাবে দূরদর্শিতার অভাবে অনেক কাজ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার সবই অদূরদর্শিতায় ভরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে দূরদর্শিতার অভাবে সেই মহতী উদ্যোগটি সাফল্যের মুখ দেখেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে পথের কাঁটা। অতএ যে কোনো উন্নয়নকর্মই হোক না কেন এর সার্বিক দিক চিন্তা না করে, পূর্বাপর জরিপ না এ উন্নয়ন কত দিন কত জনকে সুফল দেবে তা না ভেবে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এর সঙ্গে সময়, অর্থ, লোকবল প্রভৃতি জড়িত। তাই অদূরদর্শিতা নিশ্চিতভাবে উন্নয়নের অন্তরায়।
১৩ .অপরাজনীতি
রাজনীতি হলো দলীয় বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণবিষয়ক ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এর বিপরীত চিত্রই হলো অপরাজনীতি। আমাদের সমাজে এখন অপরাজনীতিরই জয়জয়কার। এক সময় দেখা যেত, সমাজের বিত্তবান পরিবারের সন্তানেরা দেশপ্রেমের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ত্যাগ, জনসেবা, দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের মনোভাব নিয়ে রাজনীতিতে পদার্পণ করতেন। এ ধরনের বিত্তবানদের সন্তানদের অনেককেই দেখা গেছে জীবনসায়াহ্নে এসে বিত্তহীন হয়ে জনসাধারণের ভালোবাসার পুঁজিকে সম্বল করে এ ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় দেখা যায়, রাজনীতির মাঠে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজি করে ফুলেফেঁপে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। এরা অবৈধভাবে আকস্মিক পাওয়া ক্ষমতা ও অর্থের দন্তে বেসামাল হয়ে অনৈতিকতার শীর্ষে পৌছে মদ, জুয়া ও নারীসম্ভোগসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হন। এদের কারণেই আজ রাজনীতি হয়ে উঠেছে অপরাজনীতি। আর এদের দাপুটে বিচরণ মূল রাজনৈতিক দলসহ দলের প্রতিটি অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে দৃশ্যমান। অপরাজনীতি যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখন জনগণের নাগরিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয় উন্নয়ন। বলতে দ্বিধা নেই, অপরাজনীতি উন্নয়নের বিশেষ অন্তরায়।
১৪. অসীম অপচার (দুর্নীতি)
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের সর্বাংশ আজ অপচার বা দুর্নীতির কবলে নিমজ্জিত। দুর্নীতির কালো হাত সমাজ জীবনের সকল দিককে গ্রাস করেছে। দুর্নীতিই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। দুর্নীতিই আমাদের সকল অর্জন এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। তাই জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধশালী ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাদেরকে অপচার বা দুর্নীতি নামক এ সর্বনাশা ও সর্বগ্রাসী সামাজিক ব্যাধির মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে
১৫..অপসংস্কৃতি
‘অপসংস্কৃতি` নিয়ে আলোচনার আগে `সংস্কৃতি` কী—সেটা জেনে নেওয়া দরকার। সংস্কৃতি হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা কোনো জাতির রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম ও সাহিত্যকে বুঝায়। ইংরেজি ‘Culture`, শব্দের বাংলা হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আরও খাঁটি বাংলা হচ্ছে `কৃষ্টি`। আর এই কৃষ্টি শব্দের অর্থ ‘কর্ষণ` বা ‘চাষ’। ষোলো শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে ‘Culture’ শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা নাচ, গান, নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদিকে বুঝি। একটা জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভিতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি স্থবির কোনো বিষয় নয়। এগিয়ে চলাই এর ধর্ম। সংস্কৃতিকে নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা যায় না। দেশ-কাল-জাতি ভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন রকম হয়। আর সংস্কৃতির বিকৃত রূপই হচ্ছে অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি মানুষের জীবনকে কলুষিত করে, চেতনাকে নষ্ট করে আর জীবনকে নাশ করে। অপসংস্কৃতি মানুষকে খারাপ কাজের দিকে টেনে নেয়। আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি তা যদি দেশকে ভালোবাসতে না শেখায়, জীবনকে প্রেমময় না করে, মানুষের প্রতি দরদি না করে, তাহলে সে শিক্ষা হলো অপশিক্ষা। আর অপশিক্ষার পথ ধরেই অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে শিকড় গেড়ে বসে। আজকের তরুণ-তরুণীদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, চালচলন দেখলেই সেটা আঁচ করা যায়। তারা দেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশি জীবনবোধে আকৃষ্ট হয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে। পাশ্চাত্যের অনুগামী হয়ে ডিসকো নাচ, গান ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মা, মাটি, মানুষ ও দেশ। যে সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে বিপথে পরিচালিত করে সেটাই হলো অপসংস্কৃতি। চাই সেটা দেশি কিংবা বিদেশি হোক। সংস্কৃতিচর্চা মানুষকে সভ্য করে তোলে। আর অপসংস্কৃতি একটি জাতিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় ৷ বলতে দ্বিধা নেই, অপসংস্কৃতি সমাজ-উন্নয়নে বড়োরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।
১৬. অপরিকল্পনা
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যে কোনো কাজকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। এর ব্যতিরেকে অপরিকল্পনার ঘেরাটোপে কাঙ্ক্ষিত কাজটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরিকল্পনা শুধু উন্নয়ন কাজে নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে কোনো কাজে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে ছয়দফা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারপর প্রতিটি রাজনৈতিক পর্বের মাধ্যমে সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। কাজগুলি হয়েছে পরিকল্পনা মোতাবেক। উন্নয়ন কাজও তেমনি। যে কোনো প্রকল্প ও উন্নয়ন কাজের প্রারম্ভিক পর্যায় হচ্ছে পরিকল্পনা গ্রহণ। পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কাজের ধরন ও প্রকৃতি, প্রকল্পের কার্যকাল, লোকবল, আনুমানিক ব্যয়, স্থান, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ। এসকল বিষয় বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এর কোনো একটির অভাব ও অনুপস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হওয়ার কথা নয়। এজন্য পত্র-পত্রিকার পাতায় দেখা যায় অনেক উন্নয়ন কাজ অপরিকল্পনার শিকার হয়ে দীর্ঘসূত্রিতায় পড়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। এই অপরিকল্পনার জের শুধু রাষ্ট্র নয়, দেশের জনগণকেও ভুগতে হয়। সেটি আর্থিকভাবে যেমন, অবকাঠামোগতভাবে, পণ্ডশ্রমের ফলে। ফলে উন্নয়ন কাজের প্রতি রাষ্ট্র ও জনগণের উন্নাসিকতা ও বিরূপ মনোভাব দেখা দিতে পারে, যা কোনো গণতান্ত্রিক ও সুস্থ সমাজে কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া অপরিকল্পনার কারণে উন্নয়ন কাজে বিড়ম্বনা ও বিঘ্নতার কারণে রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজেও তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। ফলে সামগ্রিক কাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এজন্য উন্নয়ন কাজকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অপরিকল্পনার অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় ।
১৭. অব্যবস্থাপনা
যে কোনো কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন সুব্যবস্থাপনার। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে পরিকল্পনা ও স্বপ্নকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার চাবিকাঠি। সুব্যবস্থাপনা একটি বিশেষ গুণ। এর অভাব যে কোনো কাজকে ব্যর্থ, অসফল ও বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত করতে পারে। কোনো কাজ তা ব্যক্তি হোক, সংস্থা বা রাষ্ট্র হোক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তা সফলরূপে সার্থক করার জন্য একটি সুব্যবস্থাপনা দরকার। এর মধ্যে রয়েছে লোকবল, সময়, অর্থ, কর্মপরিকল্পনা, পারম্পর্যতা প্রভৃতি। কোন কাজটি আগে হবে, কোনটি পরে, কে কোন কাজে দক্ষ, কোন কাজটি কখন করতে হবে, প্রাক্কলিত ব্যয় প্রভৃতি দিকগুলি ব্যবস্থাপনার অংশ। এগুলির অভাবই অব্যবস্থাপনা। যেমন পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় আমরা বিশেষ ব্যবস্থাপনার উদাহরণ দেখতে পাই। সার্বিক দিক থেকেই এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন কাজের নানা দিকগুলোর সমন্বয় ও সংহতি সাধন না করতে পারলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। যেমন উন্নয়ন কাজে পরিকল্পনা রয়েছে, লোকবল রয়েছে, উপকরণ রয়েছে কিন্তু সময় নেই। তাহলে সেই কাজটিকে সফল করা কঠিন। অর্থাৎ কোনো একটি কাজকে সফল করার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সার্বিক দিকগুলিকে নিশ্চিত না করতে পারাই অব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের এ রকম অনেক উন্নয়ন কাজ অব্যবস্থাপনার ঘেরাটোপে পড়ে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। সামগ্রিক কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়। এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। কোনো প্রকল্প কাজে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাব মানে দক্ষ মাঝিহীন নৌকা। কারণ তিনি জানেন না কোন কোন পর্যায়গুলি অতিক্রম করে তাকে নদী পাড়ি দিতে হবে। অতত্রব এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, অব্যবস্থাপনা উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় ।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতেই পারি, সকল `অ` জনিত অন্ধকার অপসারণ অতি জরুরি, সময়ের সঙ্গত দাবি। তা নাহলে ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, দেশ সর্বোপরি সভ্যতা অর্ধাঙ্গ অসুখে পড়ে থাকবে। যে স্মার্ট বাংলার স্বপ্ন আমাদের চোখে মুখে ঝিকিমিকি করছে সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। `অ` এর অভিশাপমুক্ত দেশ বা জাতি গঠন কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়, ব্যক্তি নির্বিশেষের কাজ। এই বাস্তবতা শিরোধার্য করেই আমাদের সকল কাজে শৈল্পিক সূর্যময় পথের ছবি আঁকতে হবে।
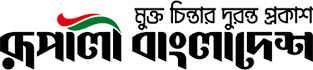






-20250415074300.webp)
-20250413175442.webp)

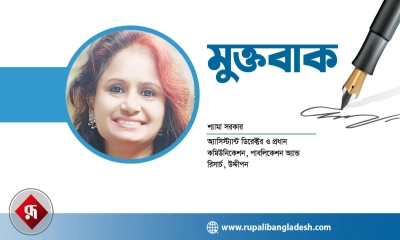
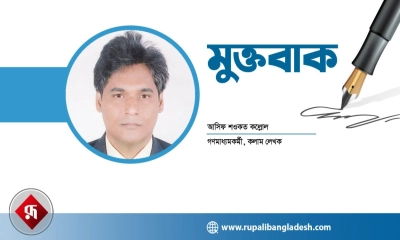
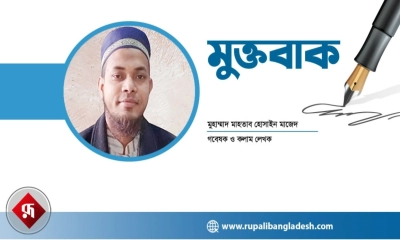







-20250418151309.webp)





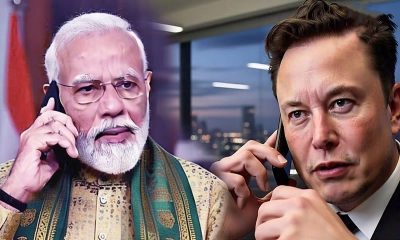

-20250418145345.webp)




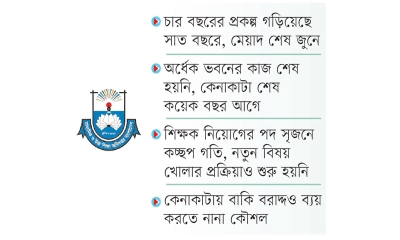
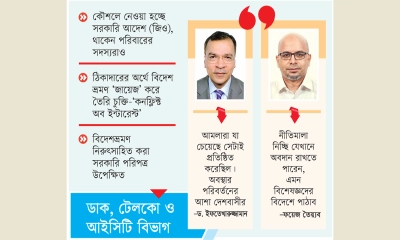









আপনার মতামত লিখুন :