সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানও কমিশনের অন্যতম সদস্য। নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটি আইন রয়েছে। ২০২২ সালের এ আইনানুযায়ী সার্চ কমিটির সদস্যরা নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করেন। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন।
আইনানুযায়ী বর্তমান সার্চ কমিটিতে আরও আছেন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. নূরুল ইসলাম এবং সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান (পিএসসি) মোবাশ্বের মোনেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম। আশা করা যায়, এ অনুসন্ধান কমিটি একদল যোগ্য ও আস্থাভাজন কমিশনারদের খুঁজে বের করতে পারবেন। এর কারণ এ অনুসন্ধান কমিটিতে কোনো দলীয় প্রভাব নেই; এবং তাদের ওপর কোনো দলীয় প্রার্থী খুঁজে বের করার তাগিদও নেই।
গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। নির্বাচন না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। নির্বাচন যে রকম গণতন্ত্রও সেরকম। গত তিনটি নির্বাচন যে রকম ছিল আমাদের তথাকথিত গণতন্ত্র সেরকমই ছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের মরণযাত্রা শুরু হয়। এরপর আরও তিনটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা পুরোপুরি গণতন্ত্রহীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হই।
সার্চ কমিটি ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে নির্বাচন কমিশনারদের নাম চেয়েছে। আইনানুযায়ী সার্চ কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী সংগঠনের কাছ থেকে নাম আহ্বান করতে পারবে। আশা করি রাজনৈতিক দলগুলো নাম প্রস্তাব করে সহযোগিতা করবে। আগামী কমিশন পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। কাজেই, এই কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।
আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে। বিগত সরকার তিন তিনটি প্রহসনের নির্বাচন করেছে। একদলীয় ও একপক্ষীয় এসব নির্বাচনের ওপর জনগণ কোনো আস্থা রাখেনি। সবশেষ হাবিবুল আউয়াল কমিশন যে নির্বাচন করেছে তা অত্যন্ত হতাশাজনক। শুধু তাই নয়, এসব নির্বাচন করার পরও কমিশনের কোনো অনুশোচনা আমরা দেখিনি। উপরন্তু এসব নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে দেখানোর জন্য তাদের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। ৫% ভোটকে ৪০% ভোট দেখানোর প্রবণতাও আমরা দেখিছি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রক্ষাপট যদিও কোটা আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেওয়ার কারণ বিগত সরকারের জুলুম নির্যাতন ও জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। ভোট কেড়ে নেওয়ার নানা কৌশল রপ্ত করে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে গত ১৬ বছরে। জনগণ সে কারণেই একটি দাবিকে সামনে রেখে গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয়। ভোটাধিকার হরণ একটি গণ-আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ দেওয়ার বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে।
শেখ হাসিনার পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে এখন রাষ্ট্র গঠন ও সংস্কার দুটোই বড় এজেন্ডা। এই সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্বাচন সংস্কার একটি বড় বিষয়। কারণ, এ সরকার নতুন কমিশন গঠন করে হয়তো একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে কিন্তু তাতে আমাদের নির্বাচন সংকটের স্থায়ী সমাধান হবে না। পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে বর্তমান সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের মাধ্যমেই নির্বাচন করতে চাইবে। ক্ষমতায় কে আসবে সেটা আমরা জানি না। তবে, বিএনপির সাম্প্রতিক বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে তারা কাল-পরশুর মধ্যেই একটি নির্বাচন চায়। বিএনপিকে বুঝতে হবে যে, শুধু একটি নির্বাচন করার জন্য এ জাতি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যোগ দেয়নি। তারা স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন যেমন চেয়েছিল তেমনি ভবিষ্যতে এদেশে যেন আর কোনো ফ্যাসিস্ট শক্তির জন্ম না হয় সেটিও চেয়েছিল। প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের অব্যক্ত কথাই এটা। সংস্কার না করে শুধু ক্ষমতার পালাবদল গণ-অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য নয়। কাজেই, রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক সব বিধিবিধান বহাল রেখে আরেকজনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সেই একই রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিধানের ওপর ভর করে নতুন ক্ষমতাশীলরাও পুরোনো ফ্যাসিস্ট রূপেই আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিটি জাতিকে অভ্যুত্থানের মর্মকথা বুঝতে হয়। বর্তমান সরকার নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে নির্বাচনী আইনের সংস্কারও জরুরি। অন্যান্য সংস্কারও জরুরি।
সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০২২ সালের আইনেরও সংস্কার লাগবে। বর্তমান আছে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার পদে কাউকে সুপারিশের ক্ষেত্রে তিনটি যোগ্যতা থাকতে হবে। তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ও বয়স হতে হবে ৫০ বছর। এছাড়া তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বিচার বিভাগীয়, আধা সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত পদে বা পেশায় কমপক্ষে ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আর যদি কেউ আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে, বা দেউলিয়া হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পেলে, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র্রের নাগরিকত্ব নিলে কিংবা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করলে তিনি কমিশনার হিসেবে অযোগ্য হবেন। নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট-১৯৭৩ বা বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস) অর্ডার-১৯৭২ এর অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলেও তিনি কমিশনার হিসেবে অযোগ্য হবেন।
দেখা যাচ্ছে, কমিশনারদের যোগ্যতার মাপকাঠি অতি সাধারণ। বয়স ৫০ আর যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেই কেউ কমিশনার বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারেন। নির্বাচনের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মাত্র এমন একজন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে না। তার আরও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। হতে পারে এগুলো প্রাথমিক যোগ্যতা। কিন্তু আরও যোগ্যতা থাকা চাই। তাই আইনে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সংযোজন থাকা উচিৎ। সবচেয়ে বড় কথা যে আইনের মাধ্যমে কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশনের মতো কমিশন গঠন সম্ভব সে আইনের অবশ্যই সংশোধন দরকার। যদিও বিদ্যমান আইনেই সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে বর্তমান সরকার যেহেতু নির্দলীয় সরকার সে কারণে তারা বিদ্যমান আইনের অধীনেই একটি নিরপেক্ষ ও আস্থাভাজন কমিশন গঠন করতে পারবেন বলে মনে করি। কিন্তু কমিশন গঠন হয়ে গেলেও বিদ্যমান আইনের সংস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে ভালো কমিশন গঠন করা যায় সে লক্ষ্যেই এর সংশোধন দরকার। নির্বাচনী সংস্কারের এটিই হবে প্রথম সংস্কার।
এছাড়া রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচনের রূপরেখা কেমন হবে সেটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালে দেশের প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ অবধি কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনেই কোনো জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। কাজেই, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়া নির্বাচনকালে পুলিশ ও প্রশাসন কার অধীনে কীভাবে কাজ করবে সেটি বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের নির্বাচনী কাঠামোতে দলীয় প্রশাসনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা যায় না। যদি সম্ভব হতো তবে বিগত সরকার তিনটি প্রহসনের নির্বাচন করত না। আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনেই ভালো নির্বাচন সম্ভব দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে। কিন্তু তারা নিজেদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করেছে। তবে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে নির্বাচনকালীন সরকারের একটি রূপরেখা প্রস্তাব করতে হবে। সেটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক বা অন্য কিছু। এটি হবে বড় একটি সাংবিধানিক সংস্কার।
রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দরকার। সে লক্ষ্যেই বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ৪৫ জন নারী সংসদ সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংসদের বিজয়ী দলই তাদের পছন্দের প্রার্থীদের সংসদে নিয়ে আসেন। বিগত সরকারের আমলে কারা সংসদে গিয়েছে তা জাতি দেখেছে। এতে যে উদ্দেশ্যে নারী প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে তা মোটেও প্রতিফলিত হয়নি। ফলে বাস্তব কারণেই সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।
নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে ভোটের কয়েকদিন আগে ও পরে মাঠে যথেষ্ট পরিমাণ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন রাখতে হয়। এ সময়ে দেশের নিয়মিত বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ ঠিকই কমিশনের অধীনে থাকে। কিন্তু তারা কাজ করে মূলত প্রশাসনের অধীনে। আবার প্রশাসনও এ সময়ে কমিশনের অধীনেই থাকে। কিন্তু প্রশাসন কাগজে কমিশনের অধীনে থাকলেও এরা সরকারেরই অংশ। কাজেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যা-ই বলা হোক না কেন প্রশাসন ও পুলিশ দুটোই সরকারের অধীনেই থাকে।
এরপরও কমিশন যদি শক্ত হাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় তাহলে কিছুটা অন্তত নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে দেখেছি কমিশন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। কমিশনকে সরকারি দলের প্রার্থীর পক্ষেই সাফাই গাইতে দেখা গেছে। এছাড়া পুলিশের সহায়তায় সামরিক বাহিনী বা বিজিবি মোতায়েন করা হলেও তারা সরাসরি সরকারের অধীনেই কাজ করে। কারণ, আইন অনুযায়ী নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কমিশনের অধীনে কাজ করবে। কিন্তু এ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সামরিক বাহিনী অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তারা সরকারের অধীনেই থাকে। এ বিষয়ে একটি যথোপযুক্ত বিধানও জরুরি।
নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে অনেক কর্মচারী-কর্মকর্তা। গত সরকারের আমলে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এসেছে। আসলে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার দায় থেকে মাঠপর্যায়ের একজন পোলিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেউ মুক্ত নন। এ দায় তাদের সবাইকেই নিতে হবে। এখন কমিশন যদি কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় তা সরকারকে কার্যকর করতে হয়। সরকার কমিশনের প্রস্তাব কার্যকর না করলে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কমিশনের অধীনে কাজ করলেও কমিশনের আদেশ গ্রাহ্য করবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
আমরা কাজী হাবিবুল আউয়াল, কে এম নূরুল হুদা বা কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদ কমিশনের মতো আর নির্বাচন কমিশন চাই না। বিগত তিনটি নির্বাচনের মতো আর নির্বাচনও দেখতে চাই না। অন্তর্বর্তীকালীন এ সরকারকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এগুলো সম্পন্ন করে দ্রুত একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে হবে। এটিই এ সকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের ভবিষ্যৎ পথ রচনা করতেও এ সরকারকে একটি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে।






-20241110103004.jpg)


-20241109043931.jpg)









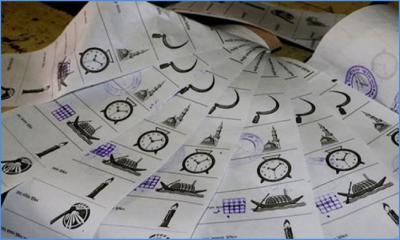





















আপনার মতামত লিখুন :